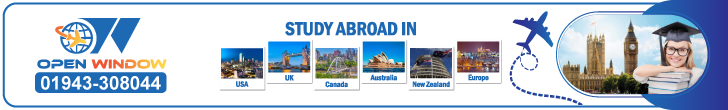মোঃ আব্দুর রহমান প্রাং : বর্তমান পৃথিবীতে অনেক দেশে রাজনৈতিক মতানৈক্য (polarization) এবং নির্বাচনের বিষয়গুলিকে ঘিরে গভীর ভাঙন দেখা দিচ্ছে। এই চক্রে সমাজ ভাগ হচ্ছে দুই—অথবা আরও অনেক—মতবাদে, এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া কেবল ভোটকেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান।
মতানৈক্যের প্রকৃতি ও কারণ: একদিকে, রাজনৈতিক দল ও তাদের সমর্থকরা অনেক ক্ষেত্রে ‘আমরা’ ও ‘তারা’ বিভাজন করেন, যার ফলে মধ্যপন্থা বা মধ্যমঞ্চের স্থান সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।
অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, তথ্যপ্রচারের প্রযুক্তি (সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অ্যালগরিদম ভিত্তিক ফিল্টার বুদ্বুদ), এবং বিভাজনমূলক রাজনৈতিক বক্তৃতা—সবই এই মতভেদের তীব্রতা বাড়িয়ে তোলে।
বিশেষ করে, নির্বাচনের সময় প্রচার ও তথ্যপ্রচারে বিকৃত বা মিথ্যা ধারণা ছড়িয়ে পড়তে পারে—তথ্যবহির্ভূত তত্ত্ব ও গুজবের প্রভাব এখন বিশ্বজুড়ে প্রবল।
অনেক দেশে বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইত্যাদির ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।
নির্বাচন ও গণতন্ত্রের অবনতি: একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা গত কয়েক বছরে ধীর গতিতে সংকুচিত হয়েছে।
নির্বাচনের মান কেবল ভোটগ্রহণেই সীমাবদ্ধ নয়—ভোটের আগে, ভোটের সময় ও পরে নানা প্রকার বাধা, ভয়-উস্কানি, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, ভোটবাতিল দাবি—সবকিছুরই নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরাজিত দল বা প্রার্থী নির্বাচন ফলাফল মেনে নিতে না চাওয়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ও দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ দেখা দেয়।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: বিপর্যয় ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক প্রবণতার প্রতিচ্ছবি বহন করছে। গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক দোলাচল, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গ্রামীণ ও শহুরে হরতাল-বিক্ষোভ (যা “July Revolution” নামে পরিচিত) সেই সংকটেরই প্রতিফলন।
প্রধান চ্যালেঞ্জ
১. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও শক্তি প্রয়োগ;
— দলগুলোর মধ্যে বিভাজন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিরোধীদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবহারের অভিযোগ বারবার উঠছে।
— “অপারেশন ডেভিল হান্ট” নামে একটি উদ্যোগ চালু হয়েছে, যার উদ্দেশ্য অবৈধ কর্মকাণ্ড দমন করা হলেও বিরোধী দল ও সমর্থকদের মতে এটি রাজনৈতিক দমন-পীড়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।
২. প্রতিষ্ঠানগত অবস্থা ও সংস্কারের দাবি;
— বাংলাদেশ এখন এক বিরল রাজনৈতিক স্থানান্তরের পর্যায়ে। প্রধানমন্ত্রীর শাসন কাঠামো নতুনভাবে রূপ নিচ্ছে, এবং নতুন সরকার গঠনের আগে আইন ও সংবিধান সংস্কারের দাবি জোরালো হচ্ছে।
— “July Charter” নামে একটি প্রস্তাবিত চুক্তি ইতিমধ্যে আলোচনায় রয়েছে, যাতে নির্বাচনী ও প্রশাসনিক সংস্কার অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
৩. সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও জনমত;
— দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবিচার মানুষের মনে হতাশা, অনিশ্চয়তা ও ভয় বাড়িয়েছে।
— ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, বিচারের নিরপেক্ষতা এবং অংশগ্রহণমূলক রাজনীতির অভাব জনগণের রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাবকে উসকে দিতে পারে।
আমার দৃষ্টিতে আশার দিক: বাংলাদেশের সামনে একটি বিশেষ সুযোগ আছে—জনগণের অংশগ্রহণ ও দাবি-প্রত্যাশার ভিত্তিতে যদি রাজনৈতিক পুনর্গঠন কার্যকরভাবে ঘটানো যায়, তবে দেশ ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী, সমতাভিত্তিক ও ন্যায্য গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে পারবে।
আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পর্যালোচনা ও সুপারিশ: নিচে কিছু ভাবনা ও সুপারিশ তুলে ধরা হলো, যা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ জনগণের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে।
ভাবনা: রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক নৈতিকতা ভেঙে গেলে গণতন্ত্র কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা ছাড়া গণতন্ত্র টেকসই নয়।
নির্বাচন কোনো একদিনের ঘটনা নয়; এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ—মনোনয়ন, প্রচারণা, ভোটগ্রহণ, ফলাফল ঘোষণা, ও পরবর্তী বিচার—স্বচ্ছ ও ন্যায্য হতে হবে।
রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব মানে কেবল “কে জয়ী” নয়; বরং “ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় সবার অংশীদারিত্ব” নিশ্চিত করা।
সুপারিশ:
১. নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা;
কোনো পক্ষের স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে।
২. ডিজিটাল প্রচারণা ও তথ্যপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ;
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গুজব, মিথ্যা তথ্য ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ঠেকাতে কঠোর ও স্বচ্ছ নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন।
৩. সাংবাদিকতা, নাগরিক অধিকার ও অংশগ্রহণ সম্প্রসারণ;
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। নাগরিক সমাজকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা জরুরি।
৪. সংস্কার ও সংলাপভিত্তিক সমঝোতা;
দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবেই, কিন্তু সাধারণ নীতিমালা ও নিয়ম নিয়ে তাদের একমত হওয়া উচিত। নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-পরবর্তী সংলাপ অপরিহার্য।
৫. শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি;
সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সচেতনতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায়। যদি রাজনৈতিক দলগুলো সংকীর্ণ স্বার্থ ছাড়িয়ে গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দেয়, তবে সাম্প্রতিক সংকটই দেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।